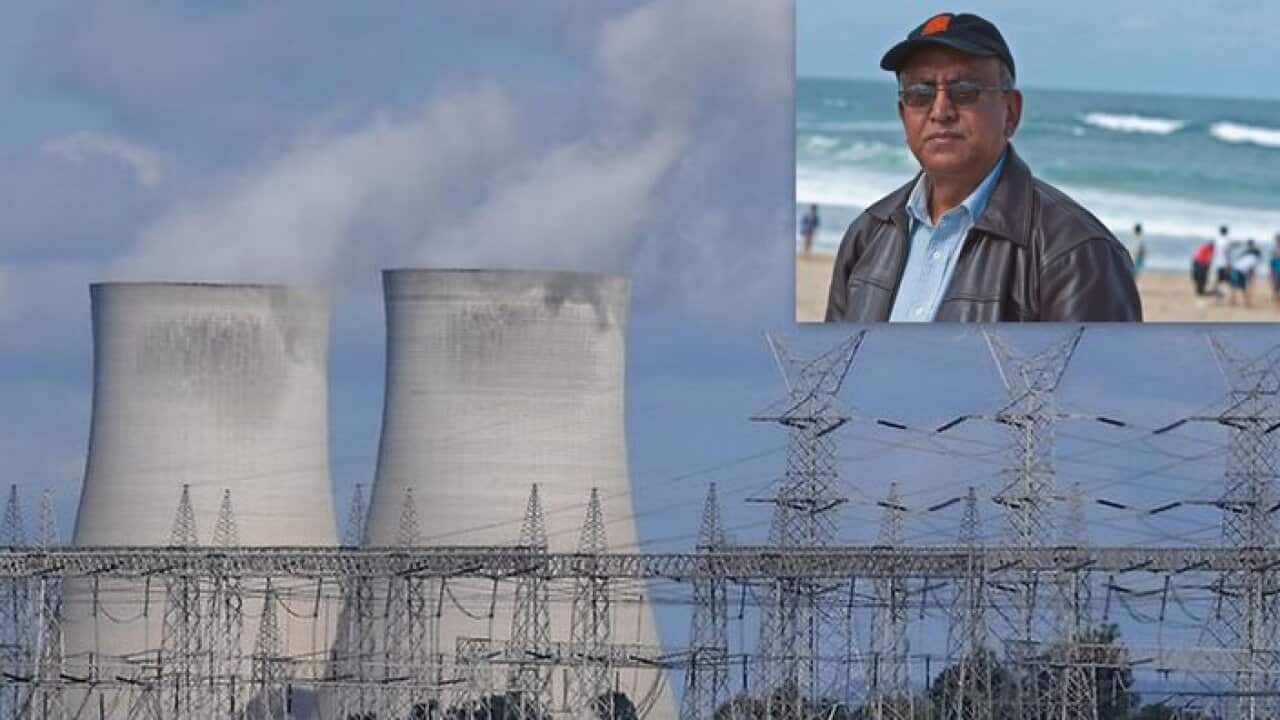বাংলাদেশের জাহাজ-ভাঙ্গা শিল্প নিয়ে এসবিএস ডেটলাইনের ভিডিও প্রতিবেদনটি দেখুন এসবিএস অন-ডিমান্ডে।
শিপ-কাটার হিসেবে দেলোয়ার হোসেনের কাজটা হয়তো ধীরে ধীরে তাকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে চলছে, কিন্তু তার সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তা—এই কাজটাই হয়তো সে হারাতে চলেছে।
যদি জুন মাসের শেষ নাগাদ তাদের স্ক্র্যাপইয়ার্ডকে গ্রিন বা পরিবেশবান্ধব ঘোষণা না করা হয়, তাহলে তার কাজ আর থাকবে না, আর থাকবে না স্ত্রী আর ছোট দুই সন্তানের মুখে খাবার তুলে দেওয়ার সামর্থ্য।
গত ২৬ জুন একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি আইনি বাস্তবতায় পরিণত হওয়ার মাধ্যমে সৈকতে থাকা চট্টগ্রামের ৯০ শতাংশের বেশি স্ক্র্যাপইয়ার্ড কার্যত অচল হয়ে পড়ার কথা।
বাংলাদেশ সরকার বলেছে, এই তারিখের পর থেকে এমন কোনো স্ক্র্যাপইয়ার্ডে পুরনো জাহাজ আমদানির অনুমতি সরকার দেবে না, যারা ‘হংকং ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দ্য সেফ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টালি সাউন্ড রিসাইক্লিং অব শিপস’-এর মানদণ্ড পূরণ করে না। এসব ইয়ার্ডকে হয় গ্রিন বা পরিবেশবান্ধব সনদ পেতে হবে, তা না হলে বন্ধ করে দিতে হবে।

বাংলাদেশ শিপ ব্রেকার অ্যান্ড রিসাইক্লারস অ্যাসোসিয়েশনের (BSBRA) সভাপতি মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম আশঙ্কা করছেন, এর ফলে প্রায় ৮০ শতাংশ শ্রমিক তাদের চাকরি হারাবে।
তিনি বলেন, “এই শিল্পে সরাসরি ৫০ হাজারের বেশি মানুষ কাজ করছে। কিন্তু এ বছর জুনের পর হয়তো ১০ হাজার শ্রমিক কাজ করতে পারবে, আর বাকি ৪০ হাজারের চাকরি থাকবে না।”
তিনি জানান, তাদের সংগঠনের ১১৪টি সদস্য স্ক্র্যাপইয়ার্ডের মধ্যে বর্তমানে মাত্র ৭টি পরিবেশগত মানদণ্ডে উত্তীর্ণ।
তাঁর আশা, বছরের শেষ নাগাদ এই সংখ্যা ২০টিতে পৌঁছাবে। তবে শিল্প বিশ্লেষকদের অনেকেই বলছেন, বাস্তবে সংখ্যা হবে তার অর্ধেক—মাত্র ১০টি।
যদিও এই শিল্পের সমালোচনাকারীরা চান, এই সংখ্যা যেন শূন্যে নেমে আসে।
চট্টগ্রাম বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর এবং স্টিলের পরিমাণ অনুযায়ী বিশ্বের শীর্ষ জাহাজ ভাঙা কেন্দ্র।
বাংলাদেশ শিপ ব্রেকার অ্যান্ড রিসাইক্লারস অ্যাসোসিয়েশনের (BSBRA) তথ্য অনুযায়ী, গত বছর বিশ্বের যেসব পুরনো জাহাজ ভেঙে ফেলা হয়েছে, তার প্রায় ৪০ শতাংশের শেষ ঠিকানা হয়েছে এই শহরের কাদামাটির সৈকতে।
এটা একদিকে যেমন পরিবেশদূষণকারী, তেমনি অত্যন্ত বিপজ্জনক একটি শিল্প হিসেবেও পরিচিত।
দেলোয়ারের মতো শ্রমিকেরা অক্সিটর্চ ব্যবহার করে বিশাল মালবাহী জাহাজ কেটে টুকরো টুকরো করে থাকেন, যাতে সেগুলোর ধাতব অংশ ও যন্ত্রাংশ স্ক্র্যাপ হিসেবে বিক্রি, পুনর্ব্যবহার কিংবা রিসাইক্লিং করা যায়।
উঁচু জায়গা থেকে পড়ে যাওয়া বা মাথার ওপর ভেঙে পড়া স্টিলের ঝুঁকি তো আছেই—এর পাশাপাশি শ্রমিকদের প্রতিনিয়ত বিষাক্ত ধুলা, ধোঁয়া আর রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসতে হয়। অনেক সময় তারা খালি পায়ে কাজ করেন, তাদের মুখে কোনো সুরক্ষামূলক মাস্কও থাকেনা।
আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন IndustriALL Global Union-এর তথ্য মতে, গত পাঁচ বছরের হিসেব অনুযায়ী বাংলাদেশি শিপব্রেকিং ইয়ার্ডে অন্তত ৩৮ জন শ্রমিক মারা গেছেন এবং আহত হয়েছেন ১৭৭ জন।

দেলোয়ার হোসেন একবার পিঠে চোট পেয়েছিলেন, আর এখন তার কাশির ধরণ বলছে, দেহের ভেতরের ক্ষয় হয়তো আরও গভীরে ছড়িয়ে পড়েছে।
“আমরা যখন জাহাজ কাটাকাটি করি, তখন চারপাশটা ধোঁয়ায় ভরে যায়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসকষ্ট আর সংক্রমণ শুরু হয়,” বলেন তিনি।
এই কষ্টসাধ্য কাজের জন্য প্রতিদিন তিনি পান মাত্র ৬০০ টাকা (৭ ডলার ৭০ সেন্ট)। তার মতে এটা যথেষ্ট নয়, এমনকি অন্য অনেক কাজের তুলনায়ও বেশ কম।
সত্যি বলতে কী, এই কাজ আমার ভালো লাগে না। কিন্তু পরিবারকে দেখভাল করতে হয়, তাই আমার আর কোনো বিকল্প নেই।
অনেক সমালোচনাকারীর মতে, বাংলাদেশের কোনো সমুদ্রসৈকতে জাহাজ ভাঙার এমন কোনও পদ্ধতি নেই যেটিকে নিরাপদ বা পরিবেশবান্ধব বলা যায়—কোনও উন্নত দেশে এধরনের কাজ অনুমোদন পেতো না।
তারা আরও বলেন, হংকং কনভেনশনটি বেশ ত্রুটিপূর্ণ এবং এই শিল্পকে দীর্ঘদিন ধরে জর্জরিত করে আসা মূল সমস্যাগুলোর—যেমন শ্রমিক অধিকারের অভাব, পরিবেশ দূষণ এবং একটি বিদ্যমান আন্তর্জাতিক চুক্তিকে এড়িয়ে চলার প্রবণতা—এসবের কোনও সমাধান দেয় না। ঐ চুক্তি মানতে হলে ধনী দেশ বা কোম্পানিগুলো বিপজ্জনক পুরনো জাহাজ বাংলাদেশে পাঠাতে পারবে না।

বৈশ্বিক সংস্থা ও এনজিওগুলোর একটি জোট, এনজিও শিপব্রেকিং প্ল্যাটফর্ম (NSP), ২০২৩ সালের এক বিবৃতিতে বলেছিল, হংকং কনভেনশন “কেবলমাত্র শিপিং কোম্পানিগুলোর স্বার্থ রক্ষা করবে” এবং এতে বাজেল কনভেনশনের মতো কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নেই। বাজেল কনভেনশন একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি, যা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিষাক্ত বর্জ্য ফেলার ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয়।
একটি পুরনো জাহাজকে যখন স্ক্র্যাপ করার উপযোগী ঘোষণা করা হয়, তখন বাজেল কনভেনশনের আওতায় সেটিকে নিজে থেকেই 'বিপজ্জনক বর্জ্য' হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়।
NSP (এনজিও শিপব্রেকিং প্ল্যাটফর্ম) বলছে, শিপিং কোম্পানিগুলো প্রায়ই বাজেল কনভেনশনের বিধিনিষেধকে এড়িয়ে যায় ‘ক্যাশ বায়ার’ ও ‘ফ্ল্যাগ অব কনভিনিয়েন্স’-এর মতো মধ্যস্থতাকারী ব্যবস্থার মাধ্যমে জাহাজের উৎপত্তি দেশকে গোপন রেখে।
তাদের ব্যাখ্যায়, ক্যাশ বাইয়ার হলো এক ধরনের মধ্যস্বত্বভোগী কোম্পানি, যারা জাহাজ কিনে সেটিকে একটি পোস্ট অফিস বক্স ঠিকানা-ভিত্তিক শেল কোম্পানির নামে ‘ট্যাক্স হ্যাভেন’ হিসেবে পরিচিত কোনো দেশে রেজিস্টার করে।

আরও বলা হয়েছে, সমুদ্র আইনে একটি জাহাজের দায়িত্ব নির্ধারিত হয় তার ফ্ল্যাগ স্টেট বা যেই দেশের নামে সেটি নথিভুক্ত, সেই দেশের উপর। এই সুযোগ নিয়ে ক্যাশ বায়াররা এমন সব দেশের পতাকা ব্যবহার করে, যেখানে সমুদ্র আইন প্রয়োগ দুর্বল বা শিথিল।
এইভাবে, অস্ট্রেলিয়া, গ্রিস বা চীনের মতো কোনো দেশের একটি শিপিং কোম্পানি তাদের পুরনো জাহাজ কোনো ক্যাশ বায়ারের কাছে বিক্রি করে দেয়—আর তারা সেটিকে স্ক্র্যাপের জন্য পাঠিয়ে দেয় বাংলাদেশে।
বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের সমুদ্রসৈকতের স্ক্র্যাপইয়ার্ডগুলো এই প্রক্রিয়ার জন্য বেশ জনপ্রিয়, কারণ এসব দেশে একটি জাহাজের জন্য ইউরোপের কড়া নিয়ন্ত্রিত ইয়ার্ডগুলোর তুলনায় প্রায় পাঁচ গুণ বেশি অর্থ দেওয়া হয়।
বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্টাল লইয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন (BELA)-এর পলিসি ও ক্যাম্পেইন কো-অর্ডিনেটর এবং এনজিও জোটের সদস্য বারীশ চৌধুরী বলেন, “[হংকং কনভেনশন] ‘ফ্ল্যাগ অব কনভিনিয়েন্স’ বা ‘ক্যাশ বায়ার’–এর সমস্যাগুলোর কোনো সমাধানই দেয় না।”
“এই ফাঁকগুলোই শেষ পর্যন্ত চুক্তিটিকে অকার্যকর করে তুলবে,” বলেন তিনি।

তার মতে, বাজেল কনভেনশন (যার একটি স্বাক্ষরকারী দেশ হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া) শিল্পোন্নত দেশগুলোকে নিজস্ব বিপজ্জনক বর্জ্য নিজেরাই ব্যবস্থাপনার আহ্বান জানায়। অন্যদিকে, হংকং কনভেনশন এই দায়িত্ব চাপিয়ে দেয় জাহাজের পতাকার দেশ এবং যেসব দেশে তা রিসাইক্লিং হয়, সেই দেশগুলোর উপর—জাহাজটির কান্ট্রি অব অরিজিনের ওপরে নয়।
“উন্নত দেশগুলো কিংবা যেসব দেশের মালিকানায় জাহাজ আছে, তাদের বর্জ্যের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়ার বদলে, এই চুক্তি সেই দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছে আমদানিকারক দেশ ও চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকারী রাষ্ট্রকে—যে দেশগুলো প্রায়শই এমন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পর্যাপ্ত সক্ষমতা রাখে না,” বলেন তিনি।
বারীশ চৌধুরী বলেন, সাগরগামী জাহাজগুলোতে অ্যাসবেস্টস, ভারী ধাতু, তেল ও ক্যানসারসৃষ্টিকারী উপাদানসহ নানা ধরনের বিষাক্ত উপাদান থাকে। আর এসবের ঝুঁকির মুখে রয়েছেন শুধু স্ক্র্যাপইয়ার্ডের শ্রমিকরাই নন, অন্যদের উপরেও এর প্রভাব পড়ে।
বিষাক্ত উপাদানের ছড়িয়ে পড়া তরল পদার্থ সাগরের পানি ও মাটি দূষিত করে, এবং এইসব বিষাক্ত উপকরণ দিয়ে তৈরি জিনিসপত্র সাধারণ মানুষের বাড়িঘর পর্যন্ত পৌঁছে যায়—ফলে স্থানীয় কমিউনিটির জন্য তৈরি হয় গুরুতর স্বাস্থ্যঝুঁকি।
“বাংলাদেশ এখনো সঠিকভাবে মিউনিসিপাল বর্জ্য সামলাতেই হিমশিম খায়, সেখানে এমন বিষাক্ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য যে বিশেষায়িত অবকাঠামো দরকার, তার অভাব তো আরও প্রকট,” তিনি বলেন।
বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৪ কোটির বেশি এবং এখানে বিশ্বের সবচেয়ে বড় শিপ ব্রেকিং শিল্প গড়ে উঠেছে—তবু একটি বিপজ্জনক বর্জ্য নিষ্পত্তি কেন্দ্র দেশে কোথাও নেই।
জহিরুল ইসলাম বলেন, বাংলাদেশ বিদেশি সহায়তায় একটি উপযুক্ত বিষাক্ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র গড়ে তোলার চেষ্টা করছে, তবে সেটি বাস্তবায়িত হতে এখনো কয়েক বছর সময় লাগবে।

তিনি যে PHP শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ডটি পরিচালনা করেন, সেটি দেশের অন্যতম বৃহৎ কনগ্লোমারেটের অংশ এবং দাবি অনুযায়ী, এটি বাংলাদেশের প্রথম ‘গ্রিন’ শিপ রিসাইক্লিং সুবিধা, যা হংকং কনভেনশনের মানদণ্ড মেনে চলে।
তিনি জানান, পরিবেশ ও শ্রমিকদের উপর প্রভাব কমাতে তারা বেশ কিছু পরিবর্তন এনেছেন—যেমন কংক্রিটের ফ্লোর, ক্রেন, ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম ও বর্জ্য ধারণ ব্যবস্থা।
তিনি স্বীকার করেন, জাহাজ থেকে আসা অ্যাসবেস্টস বর্জ্য দেশে নিষ্পত্তি করা সম্ভব নয়, তাই তা কংক্রিটে ঢেলে সাইটেই সংরক্ষণ করা হয়।
তবে সমুদ্রসৈকতে নিরাপদে জাহাজ ভাঙা যে সম্ভব নয় তা তিনি একেবারেই মানতে রাজি নন।
তবু তিনি একমত, এই শিল্পকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার দায়ভার শুধু বাংলাদেশের ওপর চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়।
“একটা জাহাজ তৈরি হয় উন্নত বিশ্বে, আর তার থেকে তারা ৩০ বছর ধরে মুনাফা তোলে,” তিনি বলেন।
আমরা সেই জাহাজটা পাই মাত্র ছয় মাসের জন্য, অথচ সব দোষ এসে পড়ে আমাদের ঘাড়ে।
এই প্রতিবেদনটি জুন, ২০২৫-এ প্রকাশিত SBS Dateline-এর একটি রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে।